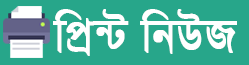১৩ এপ্রিলের রাত। রমজান মাসের প্রথম দিন। জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে ইবাদত করছিলেন কয়েকজন ফিলিস্তিনি অধিবাসী। কোনোরকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই অতর্কিত মসজিদে হামলা শুরু হলো। ঠিক কী কারণে এমন হচ্ছে সেটা বুঝে উঠতে না উঠতেই ইসরায়েল পুলিশের একটি দল মসজিদে ঢুকে পড়ে। মসজিদে যারা ছিলেন তাদের সবাইকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এক স্থানে দাঁড় করিয়ে ঘিরে রাখা হয় তাদের। মসজিদের চার কোণের মিনারে যে লাউড স্পিকার লাগানো ছিল সেগুলোর তার কেটে দেওয়া হয়।
সে রাতে কী ঘটেছিল তার হুবহু বর্ণনা করেন মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ছয়জন প্রত্যক্ষদর্শী। ওয়েস্টার্ন ওয়াল বা ওয়েলিং ওয়াল নামে ইহুদিদের পবিত্র প্রার্থনার স্থানটি আল আকসা মসজিদের একদম লাগোয়া। মৃত সৈনিকদের স্মরণে প্রতি বছর সে জায়গায় দাঁড়িয়ে জাতির উদ্দেশে বক্তৃতা দেন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট। পুলিশের আশঙ্কা ছিল, রমজান মাসে লাউড স্পিকারে আল আকসার প্রার্থনার শব্দের কারণে প্রেসিডেন্ট রুভেন রিভলিনের সেই বক্তৃতাতে সমস্যা হতে পারে। আর এ কারণেই এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে। যদিও ইসরায়েল এ কারণকে বিশ্ববাসীর সামনে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। মসজিদে হামলার ঘটনা হোক বা না হোক, এটুকু অন্তত নিশ্চিত যে এই হামলার রেশ বহু পুরনো। ১৩ তারিখের ঘটনা তো আগুনে ঘি ঢালা মাত্র। মসজিদে হামলা ছাড়াও জেরুজালেম শহরে ঢোকার ফটক দামাস্কাস গেটের সামনে একটি প্লাজা জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বহু বছর ধরে চলা ইসরাইলি অত্যাচার, দখলদারি, যুদ্ধের কারণে এ হামলার প্রেক্ষাপট যেন আগেই তৈরি করা ছিল।
১৩ তারিখের পর থেকে হামলা এখনো বন্ধ হয়নি। সোমবার ভোরেও মসজিদ প্রাঙ্গণে ইসরায়েলি বাহিনী ঢুকে ফিলিস্তিনি মুসল্লিদের ওপর রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাসের শেল ও বোমা ছোড়ে। শুক্রবার থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছিল। পূর্ব জেরুজালেমের শেখ জারাহ এলাকা থেকে ৭০টিরও বেশি ফিলিস্তিনি পরিবার উচ্ছেদের ঝুঁকির মুখে পড়ায় তা নিয়েই মূলত সপ্তাহ ধরে উত্তেজনা শুরু হয়। ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের একটি সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই পরিবারগুলোকে উচ্ছেদের পক্ষে রায় দিয়েছিল ইসরায়েলি আদালত। এর বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্টে আপিল শুনানিকে সামনে রেখে দুই পক্ষে উত্তেজনা দেখা দেয়। যদিও রবিবার মামলার শুনানি পিছিয়ে গেছে। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে নতুন তারিখ দেওয়া হবে।
এখন পর্যন্ত ইসরায়েল বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছেন প্রায় ২০০ জন। এদের মধ্যে ৫৮ জন শিশু ও নারী ৩৪ জন। আহত ব্যক্তির সংখ্যাও অনেক। গাজায় হামাস প্রধানের বাড়ি, আল জাজিরা, এপিসহ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের ভবনও গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল।
দখলদারিত্বের সূচনা
বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে বসবাসকারী ইহুদিরা ব্যাপক বিদ্বেষ-নির্যাতনের শিকার হয়। সেখান থেকেই মূলত ‘জায়নিজম’ বা ইহুদিবাদী আন্দোলনের শুরু। তাদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপের বাইরে কেবলমাত্র ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র পত্তন করা। সে সময় ফিলিস্তিন তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এটি মুসলিম, ইহুদি এবং খ্রিস্টানÑ এই তিন ধর্মের মানুষের কাছেই পবিত্র ভূমি হিসেবে বিবেচিত। এদিকে এই আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপের ইহুদিরা দলে দলে ফিলিস্তিনে গিয়ে বসত গড়তে শুরু করে। কিন্তু তাদের এই অভিবাসন স্থানীয় আরব ও মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করে। সে সময় আরব ও মুসলিমরাই ছিল সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্য কার্যত ভেঙে পড়ে। তখন যে লিগ অব নেশন গঠিত হয়েছিল, সেই বিশ্ব সংস্থার পক্ষ থেকে ব্রিটেনকে ‘ম্যান্ডেট’ দেওয়া হয় ফিলিস্তিন শাসন করার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল তখন ব্রিটেন আরব ও ইহুদি, উভয় পক্ষের কাছেই নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ফিলিস্তিন নিয়ে। কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতির কোনোটিই ব্রিটেন রক্ষা করেনি।
পুরো মধ্যপ্রাচ্য তখন কার্যত ভাগ-বাটোয়োরা করে নিয়েছিল ব্রিটেন আর ফ্রান্স। এই দুই বৃহৎ শক্তি পুরো অঞ্চলকে তাদের মতো করে ভাগ করে নিজেদের প্রভাব বলয়ে ঢোকায়। ফিলিস্তিনে তখন আরব জাতীয়তাবাদী এবং ইহুদিবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। ইহুদি ও আরব মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাখ লাখ ইহুদিকে হত্যা করার পর ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় চাপ বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে থাকা অঞ্চলটি তখন ফিলিস্তিনি আর ইহুদিদের মধ্যে ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ১৯৪৮ সালের ১৪ মে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসরায়েল। কিন্তু পরদিনই মিসর, জর্দান, সিরিয়া ও ইরাক মিলে অভিযান চালায় ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে থাকা অঞ্চলে। সেটাই ছিল প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ।
জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনে আরবদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে অঞ্চলটি বরাদ্দ করেছিল, এই যুদ্ধের পর তার অর্ধেকটাই চলে যায় ইসরায়েল বা ইহুদিদের দখলে। ফিলিস্তিনের জাতীয় বিপর্যয়ের শুরু সেখান থেকে। এটিকেই তারা বলে ‘নাকবা’ বা বিপর্যয়। প্রায় সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনিকে পালিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিতে হয়। ইহুদি বাহিনী তাদের নিজ বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে। কিন্তু আরব আর ইসরায়েলিদের মধ্যে এটা ছিল প্রথম যুদ্ধ মাত্র। তাদের মধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের সূচনা হয় তখন।
১৯৫৬ সালে যখন সুয়েজ খাল নিয়ে সংকট তৈরি হয়, তখন ইসরায়েল মিসরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কিন্তু সেই সংকটে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ব্রিটেন, ইসরায়েল আর ফ্রান্সকে পিছু হটতে হয়। ফলে যুদ্ধের মাঠে কোনো কিছুর মীমাংসা সেই সংকটে হয়নি। এরপর ১৯৬৭ সালে ৫-১০ জুন পর্যন্ত ছয় দিনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে পরবর্তী সময়ে। ইসরায়েল এই যুদ্ধে জয় পায়। তারা গাজা ও সিনাই উপদ্বীপ দখল করে নেয় যা কিনা ১৯৪৮ সাল থেকে মিসরের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্যদিকে পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিমতীরও তারা দখল করে নেয় জর্দানের কাছ থেকে। সিরিয়ার কাছ থেকে দখল করে গোলান মালভূমি। আরও পাঁচ লাখ ফিলিস্তিনিকে তাদের বাড়িঘর ফেলে পালাতে হয়।
আরব-ইসরায়েল সংঘাতের ইতিহাসে এর পরের যুদ্ধটি ‘ইয়োম কিপুর’ যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরের এই যুদ্ধের একদিকে ছিল মিসর আর সিরিয়া, অন্যপক্ষে ইসরায়েল। মিসর এই যুদ্ধে সিনাই অঞ্চলে তাদের কিছু হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করে। তবে গাজা বা গোলান মালভূমি থেকে ইসরায়েলকে হটানো যায়নি। কিন্তু এই যুদ্ধের ছয় বছর পর ঘটল সেই ঐতিহাসিক সন্ধি। মিসর প্রথম কোনো আরব রাষ্ট্র যারা ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করল। এরপর তাদের পথ অনুসরণ করল জর্দান। এতে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধ শেষ হয়নি। গাজা ভূখ- বহু দশক ধরে ইসরায়েল দখল করে রেখেছিল। সেটি ১৯৯৪ সালে তারা ফিলিস্তিনিদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। সেখানে ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বড় ধরনের লড়াই হয় ২০০৮, ২০০৯, ২০১২ এবং ২০১৪ সালে।
দুই পক্ষের দখল-বেদখলের এই লড়াইয়ে কেউ কখনোই পিছু হটেনি। হাজার হাজার যোদ্ধা, বিদ্রোহী প্রাণ দিয়েছেন। আরও সংঘবদ্ধ হয়েছে বিদ্রোহী দলগুলো। ফিলিস্তিনিরা বরাবরই দাবি করে আসছে তাদের স্বাধীন ভূমি। বিভিন্ন যুদ্ধ-বিদ্রোহে ঘর হারানো ইহুদিদের মধ্যে ফিলিস্তিনের একাংশের দখল নিয়ে এই টানাপড়েনের শুরু হয়। মুসলমানরাও তাদের স্বাধীন ভূমির দাবিতে সোচ্চার।
ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ আগ্রাসন ওই অঞ্চলে মুসলমানদের জীবন আরও জটিল ও সংকটময় করে তোলে। জেরুজালেমকে দখলে রাখতে মরিয়া ইসরায়েল। নানা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও অস্ত্রের শক্তিতে ইসরায়েলি আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের শান্তি এখন স্বপ্ন।
ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা
ইহুদিরা বিশ্বাস করে বাইবেলে বর্ণিত পিতৃপুরুষ আব্রাহাম এবং তার বংশধরদের জন্য যে পবিত্রভূমির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আজকের আধুনিক ইসরায়েল সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই অবশ্য এই ভূমি নিয়ে সংঘাত চলছে। আসিরিয়ান, ব্যাবিলোনিয়ান, পার্সিয়ান, ম্যাসিডোনিয়ান এবং রোমানরা সেখানে অভিযান চালিয়েছে, সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। রোমানরা সেখানে ‘জুডেয়া’ বলে একটি প্রদেশ তৈরি করেছিল। তবে এই ‘জুডেয়া’ প্রদেশের ইহুদিরা বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করেছেন। রোমান সম্রাট হাড্রিয়ানের আমলে ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে এক বিরাট জাতীয়তাবাদী ইহুদি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। তিনি সেটি দমন করেন। এরপর তিনি জুডেয়া এবং রোমানদের অধীন সিরিয়াকে যুক্ত করে তৈরি করেন এক নতুন প্রদেশ, যার নাম দেওয়া হয় সিরিয়া-প্যালেস্টাইন। এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সেখানে ইহুদিদের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। সেখানে ইহুদিদের ব্যাপকহারে হত্যা করা হয়। অনেকে নির্বাসিত হয়। অনেক ইহুদিকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়।
অষ্টম শতকে যখন ইসলামের উত্থান ঘটল, প্যালেস্টাইন জয় করল আরবরা। এরপর অবশ্য ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা সেখানে অভিযান চালায়। ১৫১৬ সালে এই এলাকায় শুরু হয় তুর্কি আধিপত্য। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি একনাগাড়ে শাসন করেছে তারা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর লিগ অব নেশন্স প্যালেস্টাইন তুলে দেয় ব্রিটিশদের হাতে। সেখানে ব্রিটিশ শাসন চলেছে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। কিন্তু আরব আর ইহুদিদের মধ্যে এ নিয়ে যে বিরোধ, ব্রিটিশরা তার কোনো সমাধান করতে পারছিল না। তারা বিষয়টি নিয়ে যায় জাতিসংঘে। পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য জাতিসংঘ একটি বিশেষ কমিশন গঠন করে। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইন ভাগ করার এক পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এই পরিকল্পনায় একটি আরব এবং একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল আর জেরুজালেম নগরীর জন্য একটি বিশেষ কৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়। পরিকল্পনাটি মেনে নিয়েছিল ইসরায়েল, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিল আরবরা। এই পরিকল্পনাকে আরবরা দেখছিল তাদের ভূমি কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র হিসেবে। কিন্তু প্যালেস্টাইনের ওপর ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার মাত্র একদিন আগে ইহুদিরা ইসরায়েলের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। পরের দিনই ইসরায়েল জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানাল, যা গৃহীত হয় এক বছর পর। জাতিসংঘের ১৯২টি দেশের ১৬০টি ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
ঐতিহাসিক আল আকসা মসজিদ
আল-আকসা মসজিদ অনেকের কাছে মসজিদুল আকসা বা বাইতুল মুকাদ্দাস নামেও পরিচিত। এটি ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। জেরুজালেমের পুরনো শহরে এর অবস্থান। মসজিদের সঙ্গে একই প্রাঙ্গণে কুব্বাত আস সাখরা অবস্থিত। এই পুরো স্থানকে হারাম আল শরিফ বলা হয়। বর্তমানে ইসরায়েল এ ঐতিহাসিক মসজিদটি দখল করে রেখেছে। ১৯৬৯ সালে তারা একবার আল আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগও করেছিল।
হযরত মুহাম্মদ (সা.) মিরাজের রাতে মসজিদুল হারাম থেকে আল-আকসা মসজিদে এসেছিলেন এবং এখান থেকে তিনি ঊর্ধ্বাকাশের দিকে যাত্রা করেন। এই স্থান মুসলিমদের প্রথম কিবলা। হিজরতের পর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলে কাবা নতুন কিবলা হয়। খলিফা উমর বর্তমান মসজিদের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের যুগে মসজিদ পুনর্নির্মিত ও সম্প্রসারিত হয়। এই সংস্কার ৭০৫ সালে তার পুত্র খলিফা প্রথম আল-ওয়ালিদের শাসনামলে শেষ হয়। ৭৪৬ সালে ভূমিকম্পে মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর এটি পুনর্নির্মাণ করেন। পরে তার উত্তরসূরি আল মাহদি এর পুনর্নির্মাণ করেন। ১০৩৩ সালে আরেকটি ভূমিকম্পে মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফাতেমীয় খলিফা আলি আজ-জাহির পুনরায় মসজিদ নির্মাণ করেন যা বর্তমান অবধি টিকে রয়েছে। বিভিন্ন শাসকের সময় মসজিদে অতিরিক্ত অংশ যোগ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে গম্বুজ, আঙিনা, মিম্বর, মিহরাব, অভ্যন্তরীণ কাঠামো। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করার পর তারা মসজিদকে প্রাসাদ এবং একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত কুব্বাত আস সাখরাকে গির্জা হিসেবে ব্যবহার করত। সুলতান সালাহউদ্দিন জেরুজালেম পুনরায় জয় করার পর মসজিদ হিসেবে এর ব্যবহার পুনরায় শুরু হয়। আইয়ুবি, মামলুক, উসমানীয়, সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিল ও জর্ডানের তত্ত্বাবধানে এর নানাবিধ সংস্কার করা হয়।
মসজিদুল আকসা শব্দের অর্থ হলো দূরবর্তী মসজিদ। মিরাজের রাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বোরাকে চড়ে মক্কা থেকে এখানে এসেছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে। অনেক বছর ধরে মসজিদুল আকসা বলতে পুরো এলাকাকে বোঝানো হতো এবং মসজিদকে আল-জামি আল-আকসা বলা হতো। উসমানীয় শাসনামলে প্রশাসনিক কারণে পুরো পবিত্র স্থানটি হারাম আল শরিফ বলে পরিচিত হয়।